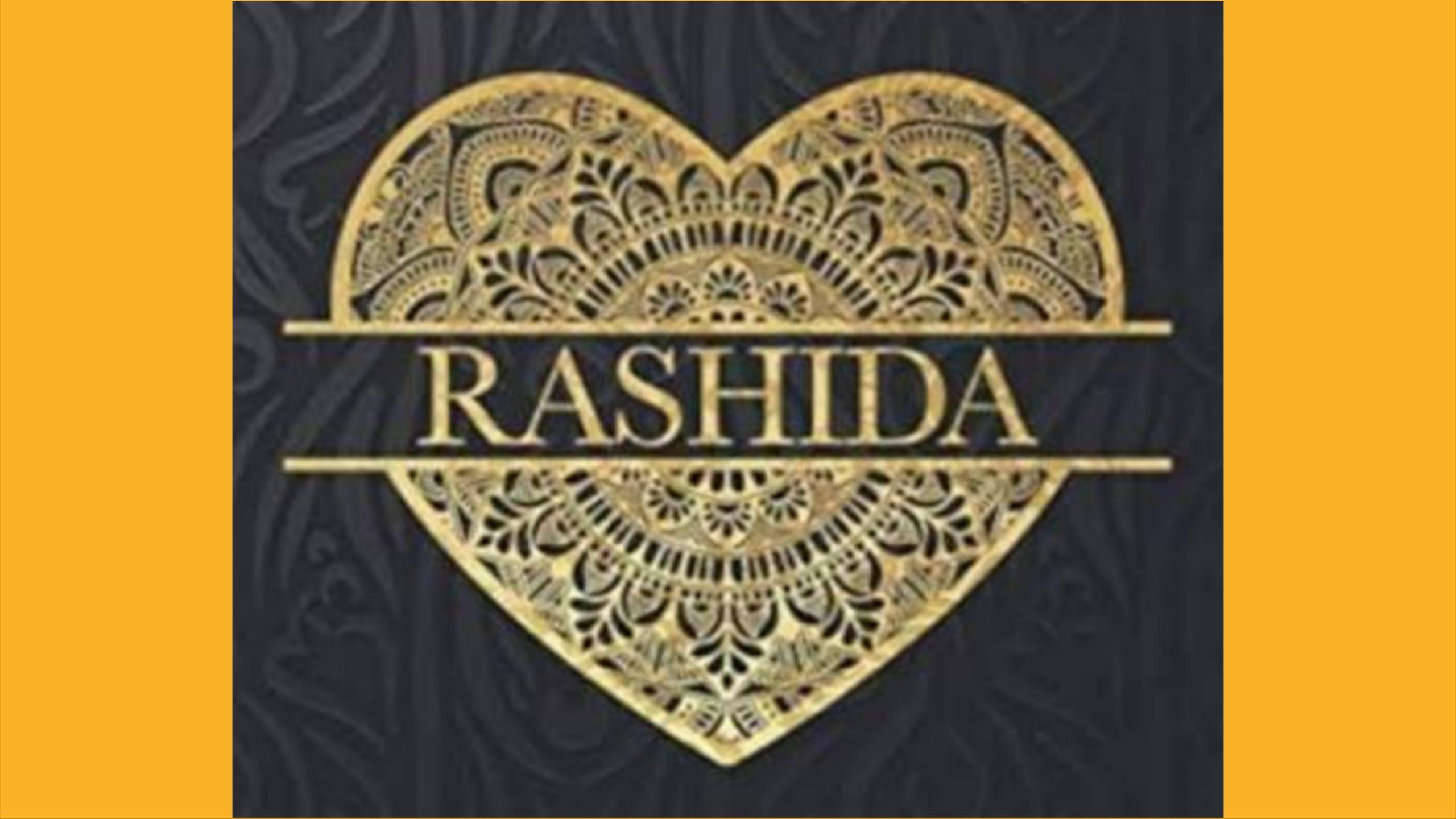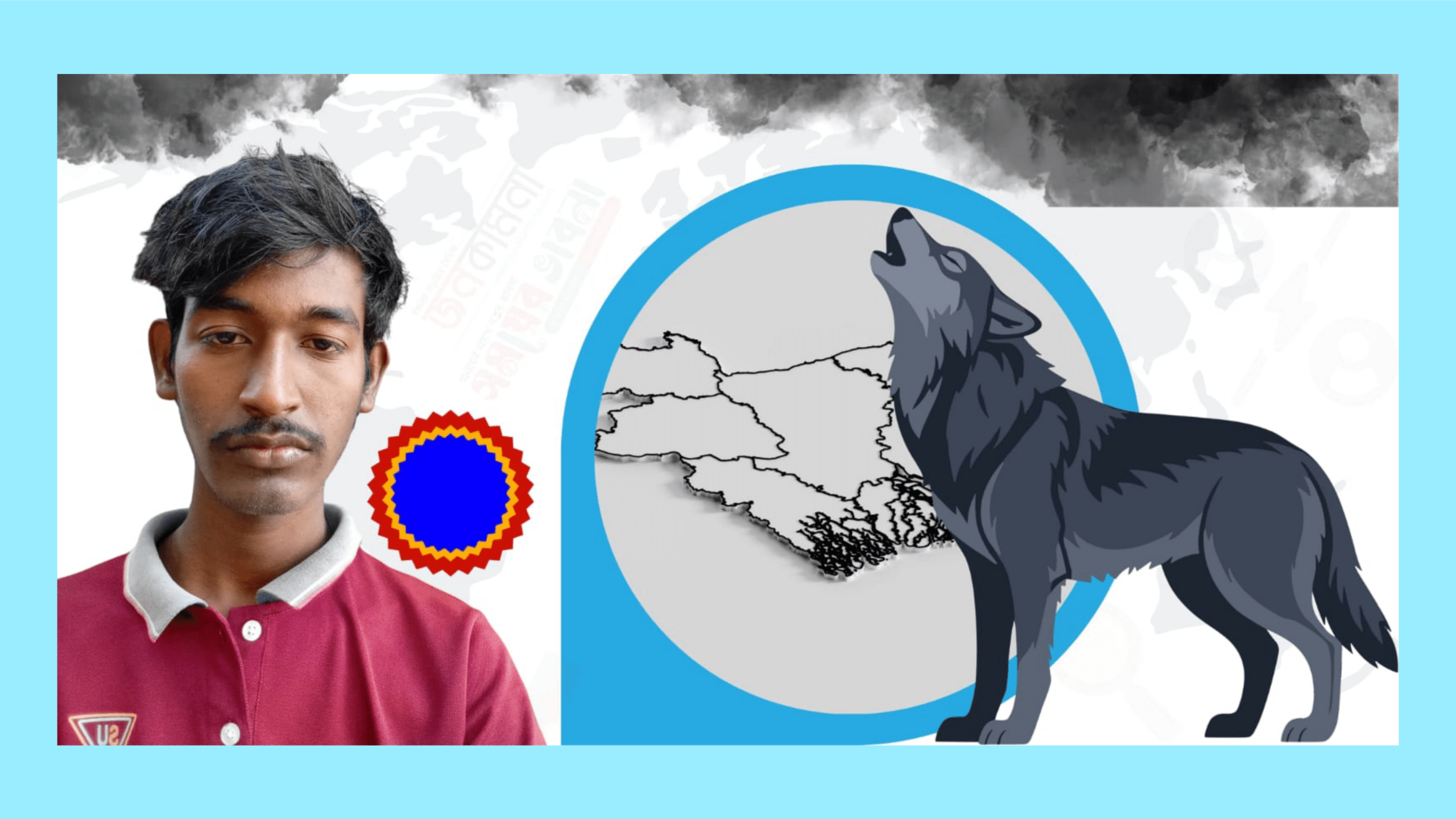প্রবন্ধ
১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের পটভূমি বুঝতে হলে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের অব্যবহিত পরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি দেওয়া অপরিহার্য। এই সময়কার সংকট ছিল মূলত একদলীয় শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যর্থতার ফলাফল, যা সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে গভীর বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। এই রচনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলি, এর রাজনৈতিক বহুমাত্রিকতা এবং পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আনীত পরিবর্তনগুলোর একটি বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের বিশ্লেষণ প্রদান করবো। এই দিনের ঘটনাকে ঘিরে বিদ্যমান সাংঘর্ষিক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার (বিপ্লব, অভ্যুত্থান, এবং হত্যাযজ্ঞ) তুলনামূলক আলোচনা এবং জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সূচিত সাংবিধানিক, অর্থনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক নবজাগরণ -এর দাবি কতটুকু যৌক্তিক, তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
পটভূমি ও ১৯৭৫ সালের সঙ্কটের বিশ্লেষণ—
- স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের রাজনৈতিক অস্থিরতা: বাকশাল প্রবর্তন ও গণতন্ত্রের অবসান–
স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের উচ্ছ্বাস দ্রুতই চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নৈরাজ্যে রূপ নেয়। তৎকালীন সরকার ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতি বাতিল করে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু হয়। এরপর ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসনব্যবস্থা (বাকশাল) প্রবর্তন করা হয়, যা সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে এবং সংবাদমাধ্যমগুলোর কণ্ঠরোধ করে। এই পরিবর্তন রাজনৈতিক বিতর্ককে দমন করে এবং ব্যাপক সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অসন্তোষ সৃষ্টি করে।
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অনুসরণ করার কথা বললেও, এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান বা প্রস্তুতি ছিল না। অপরিকল্পিত জাতীয়করণ এবং ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা দ্রুতই অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে, যার চরম পরিণতি ছিল ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষে সরকারি হিসাবেই ২৭ হাজারেরও বেশি মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায়, যা বেসরকারি মতে ১ লাখ ছাড়িয়েছিল। এই চরম অব্যবস্থা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক মহলে “তলাবিহীন ঝুড়ি” (Bottomless Basket) হিসেবে পরিচিত করে তোলে এবং জনগণের মধ্যে শাসকগোষ্ঠির প্রতি আস্থাহীনতা সৃষ্টি করে। এই পদ্ধতিগত রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতাই শেষ পর্যন্ত সামরিক বাহিনীকে রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণের সুযোগ দেয়, এবং সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরের সংঘাতকে রাজনৈতিক অস্থিরতায় রূপ দেয়।
- রক্তাক্ত আগস্টের ধারাবাহিকতা: ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থান
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপের সূত্রপাত ঘটে। এই হত্যাকাণ্ড সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড বা শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ ভাঙন ঘটায়। এরপর খুনিরা ক্ষমতা দখল করলে তাদের রাজনৈতিক মদদদাতা খন্দকার মোশতাক আহমেদের নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে।
১৫ আগস্টের খুনি চক্রকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে এবং সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ৩ নভেম্বর একটি পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটে। তবে, খালেদ মোশাররফের ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানটি একটি মারাত্মক দুর্বলতা বহন করছিল। এই অভ্যুত্থানটি দ্রুতই বিদেশি মদদপুষ্ট বা বাকশাল ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে, যা জনমনে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় এবং এক ধরনের অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। অভ্যুত্থানের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য না থাকায় এটি সহজে প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে পরাজিত হয়।
গুরুত্বপূর্ণভাবে, ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পূর্ব রাতে, ১৫ আগস্টের খুনি চক্র (মোশতাক-জিয়া বলয়ের সমর্থনে) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি জাতীয় চার নেতা—সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মুহাম্মদ মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডটি ছিল একটি সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক কৌশল, যা নিশ্চিত করেছিল যে ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান সফল হলেও, সাংবিধানিক প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধারে সক্ষম অভিজ্ঞ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব যেন রাষ্ট্রের নেতৃত্বে ফিরে আসতে না পারে। এই হত্যাকাণ্ডগুলো প্রমাণ করে যে ক্ষমতা দখলের লড়াইটি ছিল চূড়ান্তভাবে রক্তক্ষয়ী এবং রাজনৈতিকভাবে গণনা করা।
- মেজর জিয়ার নিষ্ক্রিয়তা ও সামরিক অসন্তোষ
১৫ আগস্টের পর নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান হিসেবে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান খুনিদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ফেরাতে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হন বা অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর এই নিষ্ক্রিয়তা সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে অসন্তোষকে আরও বাড়িয়ে তোলে, বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের পর জিয়াউর রহমান গৃহবন্দি হন। এই সামরিক এবং রাজনৈতিক শূন্যতাতেই ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পটভূমি রচিত হয়।
৭ নভেম্বর ১৯৭৫: সামরিক অভ্যুত্থান এবং ক্ষমতার পালাবদল
৭ নভেম্বরের ঘটনাবলি ছিল মূলত ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে একটি প্রতি-অভ্যুত্থান, যা সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিক এবং একটি “বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর” (জাসদ) উদ্যোগে ঘটেছিল। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—
- অভ্যুত্থানের কার্যকারণ ও সিপাহীদের বিদ্রোহ
মেজর জিয়াউর রহমান গৃহবন্দী হলে দেশের হাল ধরার মতো দক্ষ কেউ ছিল না। এতে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়। আরে সুযোগে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবু তাহের এবং তাঁর “বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা” সেনাবাহিনীর সাধারণ সিপাহীদের মধ্যেকার এই ক্ষোভকে কাজে লাগায়। সিপাহীরা অফিসারদের বিশেষ সুবিধা এবং সামরিক শৃঙ্খলার অভাব নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল। তাহেরের সংগঠন প্রচারপত্র বিলি করে এই অসন্তোষকে আরও উসকে দেয় এবং এটিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সংগ্রাম হিসেবে তুলে ধরে। ক্ষমতালিপ্সু কর্নেল তাহের মনে করতেন, গণমানুষের দীর্ঘমেয়াদি বিপ্লবের বদলে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে অল্প সময়েই ক্ষমতা দখল করা সম্ভব।
এই অভ্যুত্থানের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল গৃহবন্দি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা। জিয়াউর রহমান, যিনি স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে পরিচিত, সাধারণ সৈনিক এবং জনতার কাছে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলেন। অভ্যুত্থানকারীরা বিশ্বাস করত যে দেশের এই চরম বিশৃঙ্খল অবস্থায় জিয়াউর রহমানই একমাত্র ত্রাণকর্তা।
- কর্নেল তাহের (জাসদ) ও জিয়াউর রহমান: অভ্যুত্থানের দুই নায়ক
কর্নেল তাহেরের উদ্দেশ্য ছিল অভ্যুত্থানের সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে একটি বিপ্লবী জাতীয় সরকার গঠন করা এবং জাসদের সমাজতান্ত্রিক, সামরিক-বেসামরিক রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। কর্নেল তাহের এই অভ্যুত্থানকে ক্ষমতা দখলের একটি শর্টকাট পদ্ধতি হিসেবে দেখতেন।
অন্যদিকে, গৃহবন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়েই জিয়াউর রহমান কৌশলগতভাবে তাহেরের এই গতিশীলতাকে ব্যবহার করেন। জিয়াউর রহমান ঐতিহ্যবাহী সামরিক অনুক্রম এবং শৃঙ্খলার পুনরুদ্ধারে বিশ্বাসী ছিলেন, তাহেরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী দাবি বা জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাবের প্রতি তাঁর কোনো সমর্থন ছিল না।
৭ নভেম্বর সকালে জিয়াউর রহমান মুক্ত হয়ে বেতারে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। উনার এই ভাষণে জেগে ওঠে বাংলার আপামর জনতা। তিনি জনগণকে শান্তি বজায় রেখে যার যার দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। এই ঘোষণা দেশজুড়ে বিরাজমান চার দিনের দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটায়। জিয়াউর রহমানের মুক্তির পর ঢাকার রাস্তায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিপাহী-জনতার মিছিল দেখা যায়। এই আপাত জনসমর্থন এবং সংহতিই অভ্যুত্থানটিকে “জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস” হিসেবে চিহ্নিত করার ভিত্তি তৈরি করে।
পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, যদিও অভ্যুত্থানের পর ঢাকায় সিপাহী-জনতার সংহতি দেখা গিয়েছিল, কিন্তু এই দিনের মূল ঘটনাপ্রবাহ এবং রক্তপাত ক্যান্টনমেন্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জনগণের অংশগ্রহণ ছিল মূলত বিশৃঙ্খলার অবসানে জিয়ার প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে আনন্দ উল্লাস, যা জাসদ/তাহেরের বিপ্লবী আদর্শের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত ছিল না। কিন্তু অভ্যুত্থানকে দ্রুত ‘বিপ্লব’ হিসেবে রাজনৈতিকভাবে তুলে ধরার জন্য এই সংহতির চিত্র অপরিহার্য ছিল।
জিয়ার সফলতা মূলত তাঁর কৌশলগত অবস্থান থেকে এসেছিল। তিনি একদিকে তাহেরের নেতৃত্বাধীন ভারত-বিরোধী, সমাজতন্ত্র-প্রবণ সিপাহীদের সমর্থন পেয়েছিলেন, অন্যদিকে তিনি সামরিক বাহিনীর ঐতিহ্যবাহী অফিসার কোরের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিলেন, যারা জাসদের উগ্র বিপ্লবী উপাদান থেকে সেনাবাহিনীকে রক্ষা করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ এই বিভেদ দূর করতে পারতেন। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকে “বিদেশি মদদপুষ্ট” হিসেবে প্রচার করে , ৭ নভেম্বরের ঘটনাকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা জাতীয়তাবাদী সংস্থা গুলোর কাছে এই অভ্যুত্থানকে দ্রুত বৈধতা প্রদান করে।
হত্যাযজ্ঞ ও রক্তপাত এবং চেইন অব কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠা
৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানটি যেমন জিয়াউর রহমানের উত্থান এবং ক্ষমতার সংহতকরণকে চিহ্নিত করে, তেমনি এটি সেনানিবাসে ঘটে যাওয়া রক্তক্ষয়ী হত্যাকাণ্ড এবং পরবর্তীকালে কর্নেল তাহেরের বিচারের মাধ্যমে একটি ঐতিহাসিক কলঙ্কেও পরিণত হয়। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—
- মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা হত্যাকাণ্ড
৬ নভেম্বর রাত থেকে ৭ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত ঢাকা সেনানিবাসে চরম বিশৃঙ্খলা ও নারকীয় তাণ্ডব শুরু হয়। কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা এবং জিয়াউর রহমানের প্রতি অনুগত পাকিস্তানপন্থী উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদের একটি অংশ এই হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠেন। এই রাতের আক্রমণে একজন নারী চিকিৎসকসহ ১৩ জন কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়।
৭ নভেম্বর সকালে নিহত হন মুক্তিযুদ্ধের তিন পরাক্রমশালী সেক্টর কমান্ডার: ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফ, কর্নেল এ.টি.এম. হায়দার এবং কর্নেল নাজমুল হুদা। যদিও জিয়াউর রহমান খালেদ মোশাররফ ও তাঁর সঙ্গীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে জানা যায় , তবুও উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকেরা ক্যাপ্টেন আসাদ ও ক্যাপ্টেন জলিলের মতো তরুণ অফিসারদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ব্রাশফায়ারে তাঁদের হত্যা করে।
সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে উচ্চমাত্রার দলীয় বিভাজনের ফলে ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কেবল প্রধান সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের শারীরিক অপসারণের মাধ্যমেই সম্ভব ছিল। খালেদ মোশাররফ গোষ্ঠীর হত্যাকাণ্ড এবং পরবর্তীকালে তাহেরের মৃত্যুদণ্ড সামরিক অনুক্রমের মধ্যে একটি একক, প্রশ্নাতীত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য শুদ্ধিকরণ হিসেবে কাজ করেছিল। এ কারণে আওয়ামী লীগ ও প্রগতিশীল দলগুলো এই দিনটিকে ‘মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হত্যা দিবস’ হিসেবে পালন করে।
- মেজর জিয়া কর্তৃক কর্নেল তাহেরের বিচার
জিয়াউর রহমান বন্দিদশা থেকে মুক্ত হওয়ার পর কর্নেল তাহের ও জাসদের পক্ষ থেকে কিছু অযৌক্তিক দাবি-দাওয়া পেশ করেন। যার ফলে মেজর জিয়া সেই দাবিগুলো প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি দ্রুত সেনাবাহিনীকে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নেন। এতে কর্নেল তাহের নিজের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হওয়ায় তিনি মেজর জিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করতে থাকেন। এতে মেজর জিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে কর্নেল তাহেরকে ১৯৭৫ সালের ২৪ নভেম্বর রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও সামরিক বিদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার করেন। ১৯৭৬ সালের ২১ জুন গোপন সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু হয়। এই সামরিক ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন কর্নেল ইউসুফ হায়দার, যিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে পাকিস্তানিদের সহযোগিতা করেছিলেন। কর্নেল তাহের (বীর উত্তম) কে ১৯৭৬ সালের ২১ জুলাই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এই মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে সামরিক নেতৃত্বের উপর জিয়াউর রহমানের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। তবে উল্লেখ্য যে, তখন চলমান সংকট দ্রুত অপসারণের জন্য মেজর জিয়া তড়িঘড়ি করে কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দেন।
- প্রহসনের ফাঁসি: হাইকোর্টের রায় ২০১১ সালে
আওয়ামী লীগ সরকার সে বিচারকের প্রশ্নবিদ্ধ করতে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ২০১১ সালের ২২ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ রায় প্রদান করে যে কর্নেল তাহেরের বিচার ছিল একটি “সামরিক প্রহসন” এবং তাঁর ফাঁসি ছিল “ঠান্ডা মাথায় খুন”। আদালতের রায়ে কর্নেল তাহেরকে ‘প্রকৃত দেশপ্রেমিক’ হিসেবে পুনর্বহাল করা হয় এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানকে এই ঘটনার ‘মূল খলনায়ক’ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়।
জিয়াউর রহমান কর্নেল তাহেরের বিচারের ক্ষেত্রে একটি বৈধ, বেসামরিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে গোপন সামরিক ট্রাইব্যুনাল ব্যবহার করেন। এই আইনি ত্রুটি তাঁর শাসনের একটি দীর্ঘমেয়াদি দুর্বলতা তৈরি করেছিল। ২০১১ সালের আদালতের রায় সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত রাজনৈতিক সাফল্যের বিপরীতে আইনি ও নৈতিক বিচারের মানদণ্ডকে প্রতিষ্ঠা করে।
রাষ্ট্রীয় নবজাগরণ: সাংবিধানিক ও আইনি রূপান্তর
৭ নভেম্বরের ঘটনার পর, জিয়াউর রহমান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন। এই পরিবর্তনগুলোই ‘বাংলাদেশের নবজাগরণের’ অন্যতম ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—
- সামরিক শাসন জারি ও মেজর জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা বৈধকরণ
জিয়াউর রহমান পর্যায়ক্রমে সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন এবং পরে সফলভাবে নিজেকে সামরিক শাসক থেকে বেসামরিক রাষ্ট্রনায়কে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। এই ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপ নেন (রাজনৈতিক দল বিধি, ১৯৭৬), যা বাকশাল-পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগকে নিজ নামে রাজনীতিতে ফিরে আসার সুযোগ দেয়। তবে এই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার প্রাথমিক পর্যায়ে সামরিক আইনের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী ও এর আইনি প্রভাব
জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনি পদক্ষেপ ছিল সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী (১৯৭৯)। এই সংশোধনী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক আইন জারি করে নেওয়া সকল ঘোষণা, আদেশ ও বিধিকে (যার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার রুদ্ধকারী ইনডেমনিটি অধ্যাদেশও ছিল) অনুমোদন ও সমর্থন প্রদান করে, যা আইনি বৈধতা এনে দেয়। তবে, সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকারী শাসকের অবৈধ কাজগুলোকে এই সংশোধনী আইনি বৈধতা দিলেও, পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট এই পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করে বাতিল করে দেয় (২০০৯/২০১১)। এই বিষয়টি প্রমাণ করে যে জিয়ার শাসনের নবজাগরণ আইনিভাবে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের দায়মুক্তি প্রদানের ওপর নির্ভরশীল ছিল, যা সাংবিধানিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব পায়নি।
- “বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ” প্রবর্তন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তন
জিয়াউর রহমান ভাষাভিত্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ “বাঙালি জাতীয়তাবাদ”-এর বিপরীতে “বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ” প্রবর্তন করেন। এই নতুন ধারণা জাতিগত পরিচয়ের বাইরে গিয়ে ভূখণ্ড, নাগরিকত্ব এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রীয় পরিচয় প্রদান করে। এই মতাদর্শ নতুন রাজনৈতিক দল বিএনপির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী পাল্টা-আখ্যান তৈরি করে।
- সংবিধানের মূলনীতিতে পরিবর্তন
জিয়াউর রহমান সংবিধানে মৌলিক পরিবর্তন আনেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে বাদ দেন এবং রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিধান সরিয়ে দেন। সকল দলগুলো মিলে একটি নতুন সমৃদ্ধশালী দেশ গঠনের কাজে মনোনিবেশ করেন। এর ফলে জামায়াতে ইসলামী রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ পায়। সংবিধানের শুরুতে “বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম” (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি) সংযোজন করা হয়।
এই সাংবিধানিক এবং আদর্শিক পরিবর্তনগুলো ছিল একটি সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক কৌশল। এই পদক্ষেপগুলো একই সাথে পূর্ববর্তী বাকশাল সরকারকে “ধর্মনিরপেক্ষ একনায়কতন্ত্র” হিসেবে নিন্দিত করে এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের ধর্মীয় চেতনাকে কাজে লাগিয়ে রক্ষণশীল অংশগুলোর সমর্থন লাভ করে। এর মাধ্যমে জিয়াউর রহমান আওয়ামী লীগ থেকে তার রাজনৈতিক দূরত্ব স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত করেন এবং ৭ নভেম্বরের “সার্বভৌমত্ব রক্ষার বিপ্লব”-কে নতুন সাংবিধানিক কাঠামোতে সুসংহত করেন। এতে করে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত হন।
অর্থনৈতিক দর্শন ও সংস্কার: নবজাগরণের ভিত্তি
৭ নভেম্বর পরবর্তী জিয়াউর রহমানের প্রশাসন বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিপথকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়। এই অর্থনৈতিক সংস্কারগুলোই নবজাগরণের দাবির মূল চালিকাশক্তি। এরকম একটি গণজাগরণই যেন প্রয়োজন ছিল একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত, দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য। উল্লেখ্য যে বাকশাল সরকারের সময়ে দুর্ভিক্ষে বহু মানুষ মারা গিয়েছিল। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—
- সমাজতান্ত্রিক মডেল থেকে বাজার অর্থনীতির দিকে যাত্রা
জিয়াউর রহমানের প্রশাসন ১৯৭২ সালের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে দেশের দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং বিপুল জনসংখ্যা মোকাবেলার জন্য অনুপযোগী বলে গণ্য করে। তিনি দ্রুতই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি থেকে সরে এসে ব্যক্তিখাতের প্রাধান্যসহ একটি মিশ্র অর্থনীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। এই নতুন অর্থনৈতিক দর্শন উৎপাদনের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়, যা “উৎপাদনের রাজনীতি” নামে পরিচিত হয়। এই অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রথম দিকের ব্যর্থ, অপরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক নীতির কারণে সৃষ্ট আদর্শিক শূন্যতাকে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি নিজে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে ছিলেন , অংশ নিয়েছিলেন জন উন্নয়নমূলক কাজে। যা তার জনপ্রিয়তাকে আকাশচুম্বীতে পরিণত করে।
- জিয়াউর রহমানের ১৯–দফা কর্মসূচি: মূল উদ্দেশ্য ও জনমুখী নীতি
১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল জিয়াউর রহমান তাঁর রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে ১৯-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল জনগণের মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য) পূরণ করা।
এই নীতিগত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে জিয়াউর রহমান একটি সামাজিক গণতান্ত্রিক বা মধ্য-বাম ধারা অনুসরণ করেছিলেন, যেখানে উদার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা হলেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। এর পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন নীতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়, যা সেসময় ইউরোপীয় মধ্য-বাম দলগুলোর আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল বলে মনে করা হয়।
- গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বারোপ: খাল খনন কর্মসূচি
জিয়াউর রহমান গ্রামীণ অর্থনীতিকে উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে দেখেন। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানো, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং জনগণের স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বৃহৎ ‘খাল খনন কর্মসূচি’ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন। এই কর্মসূচিতে জিয়াউর রহমান নিজে কোদাল হাতে জনগণের সঙ্গে মিশে যান, যা তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ায় এবং সামরিক পটভূমির পরও তাঁকে একজন মাঠের জনদরদী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এই ‘উৎপাদনের রাজনীতি’ একই সঙ্গে উন্নয়নমূলক কাজ এবং রাজনৈতিক সংহতির কৌশল হিসেবে কাজ করেছিল। তবে, সমালোচকরা এই সময়ের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। একটি প্রতিবেদন অনুসারে, যদিও জিয়ার শাসনামলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বলা হয় , কিন্তু ১৯৭৫ সালের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় খাদ্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার কমে যায় এবং ১৯৭৩-৭৪ সালের ৪৪ শতাংশ থেকে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী গ্রামীণ মানুষের সংখ্যা ১৯৮১-৮২ সালে ৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়।
- আধুনিক শিল্পের ভিত্তিপ্রস্তর: তৈরি পোশাক শিল্প
অর্থনৈতিক নবজাগরণের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায় তৈরি পোশাক শিল্প (RMG) খাতে জিয়াউর রহমানের দূরদর্শী পদক্ষেপে। প্রায় পাঁচ দশক আগে, ১৯৭৮ সালের ৪ জুলাই, তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার দেইউ-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রামে দেশ গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠার চুক্তি করেন। এটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প। তিনি ১৩০ জন তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠান। এই শিল্পের বিকাশে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত উদ্ভাবন ছিল স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ স্কিম চালু করা, যার মাধ্যমে রপ্তানিকারকরা শুল্কমুক্তভাবে কাঁচামাল আমদানি করার সুযোগ পায়। এই নীতিটি বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পকে দ্রুত একটি প্রধান রপ্তানি খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, যা আজ দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস। এই বাস্তববাদী শিল্পভিত্তিক নীতিগত সিদ্ধান্তই বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছে।
পররাষ্ট্রনীতিতে কৌশলগত ভারসাম্য ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অবস্থান
৭ নভেম্বরের ঘটনার পর জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি ছিল কৌশলগত ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার মূল লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বহিরাগত প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—
- জোট নিরপেক্ষতা ও সবার সাথে বন্ধুত্ব নীতি অনুসরণ
জিয়াউর রহমান “ব্লক-নিরপেক্ষতা” বা “Non-alignment” নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এটি ছিল পূর্ববর্তী সরকারের ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ঘনিষ্ঠ সামরিক-রাজনৈতিক নির্ভরতা থেকে সরে আসার একটি সচেতন কৌশল। জিয়া বিশ্বাস করতেন যে একটি বা দুটি দেশের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রেখে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব নয়।
- আঞ্চলিক আধিপত্যবাদ মোকাবিলা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা
জিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে আঞ্চলিক আধিপত্যবাদকে সুকৌশলে মোকাবিলা করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ৭ নভেম্বরের পর জনমনে সৃষ্ট ধারণা ছিল যে ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানটি ভারত সমর্থিত ছিল। তাই জিয়াউর রহমান দৃশ্যত পূর্ববর্তী সরকারের ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি সম্পর্কে মিথ্যা অপপ্রচার না চালালেও আকারে-ইঙ্গিতে এটিকে ভারতের নিকট ‘দাসত্ব’ হিসেবে আখ্যায়িত করে তার নিজস্ব সার্বভৌমত্বের পক্ষে অবস্থান নেন। তাঁর কৌশলের মূল লক্ষ্য ছিল নিশ্চিত করা যে বাংলাদেশের অবস্থান যেন সিকিম, ভুটান বা পশ্চিমবঙ্গের মতো না হয়।
জিয়াউর রহমানের এই আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন তার ঘরোয়া শাসনের বৈধতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য ছিল। বাহ্যিকভাবে ভারতীয় প্রভাবের প্রত্যাখ্যান এবং ইসলামিক বিশ্বের সাথে সংহতি বৃদ্ধির মাধ্যমে তিনি ৭ নভেম্বরের মূল দাবি (সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা) জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন।
- মুসলিম রাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন
জিয়াউর রহমান মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পর্ক জোরদার করেন। ১৯৭৬ সালের মে মাসে তিনি ইসলামিক কনফারেন্স সংস্থার অধিবেশনে যোগদান করেন। এই নীতি অভ্যন্তরীণভাবে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি প্রবর্তনের সাংবিধানিক পরিবর্তনের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এতে করে কেউ কেউ মনে করে— “তাঁর ক্ষমতা দখলের নেপথ্যে পাকিস্তান, চীন এবং সৌদি আরবের রাজনৈতিক বলয়ের সমর্থন ছিল।”
একইসঙ্গে, তিনি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এবং এডিবি’র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেন। এই অর্থনৈতিক সহযোগিতা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে।
- সার্ক (SAARC) গঠনের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা
জিয়াউর রহমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক অবদানগুলোর মধ্যে একটি হলো আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট সার্ক (SAARC) গঠনের ধারণা প্রদান। এই উদ্যোগটি কেবল আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়নি; এটি ছিল দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলোর একটি কৌশল, যার মাধ্যমে বহুপাক্ষিক সংলাপকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে আঞ্চলিক প্রভাবশালী শক্তির (ভারত) একতরফা প্রভাবকে কাঠামোগতভাবে সীমিত করা যায়।
৭ নভেম্বরের উত্তরাধিকার ও আধুনিক বাংলাদেশের ভিত্তি
৭ নভেম্বরের ঘটনাবলি এবং তার পরবর্তী জিয়াউর রহমানের উত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেছে। এই দিনটি দেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির স্থায়ী ভিত্তি স্থাপন করেছে। নিম্নে সিপাহী বিপ্লবের পরে মেজর জিয়ার অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।
- রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের বিতর্কিত ও অসামান্য অবদানসমূহের বিশ্লেষণ
জিয়াউর রহমান একজন বিতর্কিত সামরিক শাসক এবং দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক, উভয় হিসেবেই পরিচিত। একদিকে তিনি কর্নেল তাহের এবং ১৯৭৭ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর শত শত সেনাসদস্যকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে সামরিক শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অন্যদিকে, তিনি বাকশাল-এর একদলীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে বহু-দলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন, অর্থনৈতিক নীতিতে আমূল পরিবর্তন আনেন এবং ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’-এর মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেন।
জিয়াউর রহমান দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রের কিনারা থেকে ফিরিয়ে এনেছেন এমনটা যেমন বলা হয় , তেমনি তাঁর শাসন ক্ষমতাকে সাংবিধানিক অবৈধতা (পঞ্চম সংশোধনী) এবং সামরিক শক্তির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- রাজনৈতিক বহুমুখীতার সূচনা
৭ নভেম্বর এবং তার ধারাবাহিকতায় জিয়াউর রহমানের উত্থান দেশের রাজনৈতিক মেরুকরণকে স্থায়ীভাবে সংহত করে। তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন, যা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে একটি শক্তিশালী, অ-ধর্মনিরপেক্ষ এবং বাজারমুখী বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই দুটি দলের মধ্যেকার বিভাজনই আধুনিক বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য।
৭ নভেম্বরের ঘটনাটি নিজেই একটি স্থায়ী, সাংঘর্ষিক প্রতিষ্ঠাতা মিথ হয়ে রয়েছে। এই দিনটিকে ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলোর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা (বিপ্লব ও সংহতি দিবস, সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান দিবস, এবং মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হত্যা দিবস) প্রচলিত আছে। ইতিহাসের এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ইতিহাস গঠনে বাধা দেয় এবং দেশের রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতাকে দীর্ঘায়িত করে।
উপসংহার:
৭ নভেম্বর ১৯৭৫ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের গতিপথকে মৌলিকভাবে বদলে দেয়। এটি দেশকে সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতি থেকে সরিয়ে এনে একটি অধিকতর বাস্তববাদী, বাজার-ভিত্তিক এবং ধর্মীয়ভাবে সহনশীল (Religiously Accommodating) রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এই পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং বাহ্যিক প্রভাব থেকে রক্ষার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। জিয়াউর রহমানের শাসনকালের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব হলো সাংঘর্ষিক নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা হলেও কঠোর সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন করা; অর্থনৈতিক উদারীকরণ শুরু হলেও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা; এবং ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবর্তে ভূখণ্ড ও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রচার করা। এই জটিল, স্ববিরোধী ভিত্তি আধুনিক বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে। তবে, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফসহ মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের হত্যা এবং কর্নেল তাহেরের বিচারের নামে প্রহসনে ফাঁসিতে হত্যার ঘটনাগুলো এখনও অমীমাংসিত আইনি ও নৈতিক প্রশ্ন হিসেবে রয়ে গেছে। ঐতিহাসিকভাবে এই সত্যগুলোর উন্মোচন এবং আনুষ্ঠানিক বিচার বা একটি জাতীয় সত্য উদ্ঘাটন কমিশন গঠনের মাধ্যমে সাংঘর্ষিক আখ্যানগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ন্যায়বিচারের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এই আইনি ও নৈতিক প্রশ্নগুলোর নিরসন ছাড়া ৭ নভেম্বরের জটিল ঐতিহাসিক ক্ষত পুরোপুরি নিরাময় করা সম্ভব নয়। পরিশেষে এটা বলা যায় যে —মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান দুর্ভিক্ষ পীড়িত ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের জন্য একজন শান্তির দূত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জন্য একটি রহমত স্বরূপ ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। আল্লাহ উনার নেক আমলসমূহ কবুল করুন এবং গুনাহ সমূহ মাফ করুন।
@bvg-wVKvbv@
‡gv: Avey e°vi wmwÏK (Rwb miKvi)
`wÿY mvjbv, MvRxcyi|
‡gvevBj:-01739-029234;
B-‡gBj:- jony90siddique@gmail.com

 Reporter Name
Reporter Name